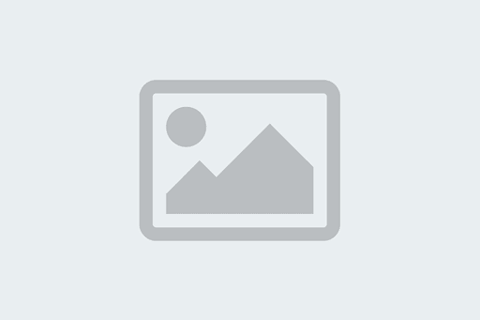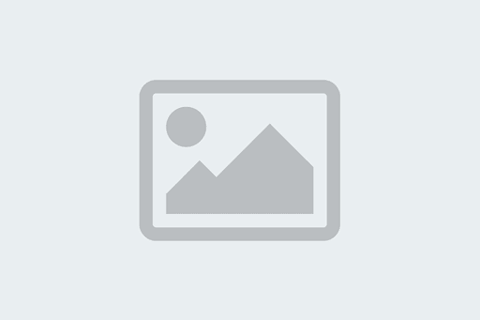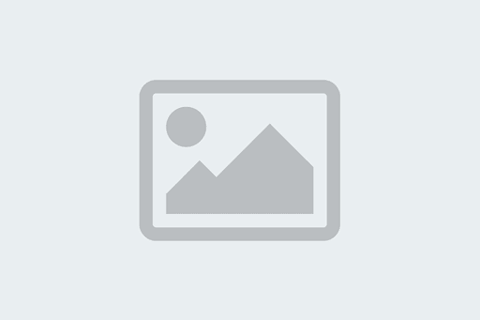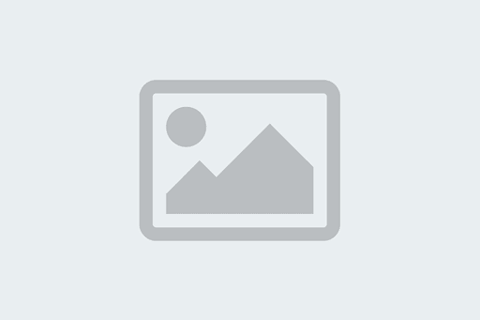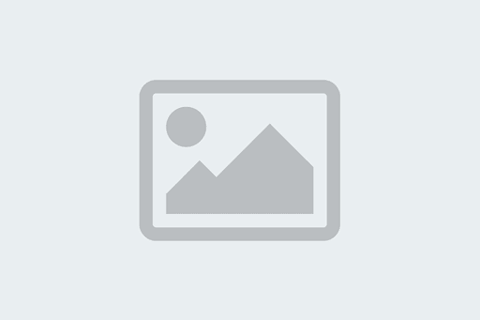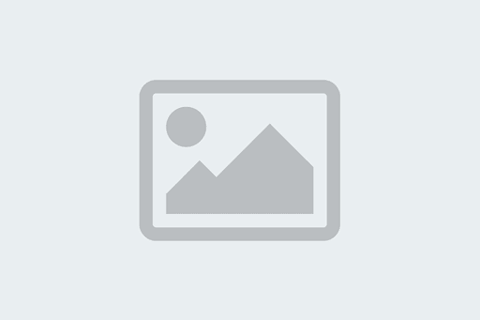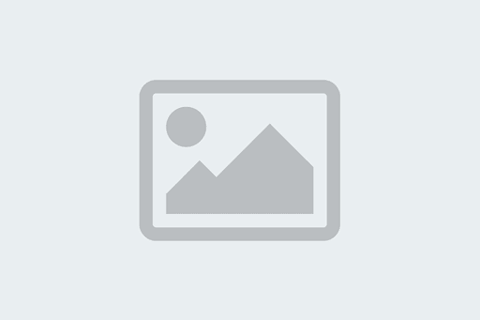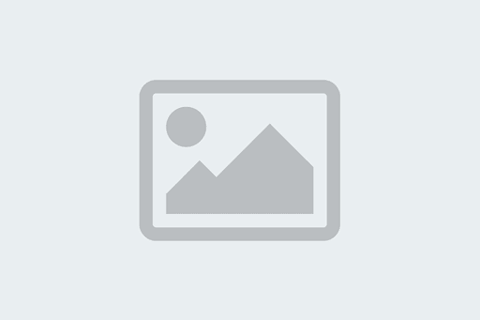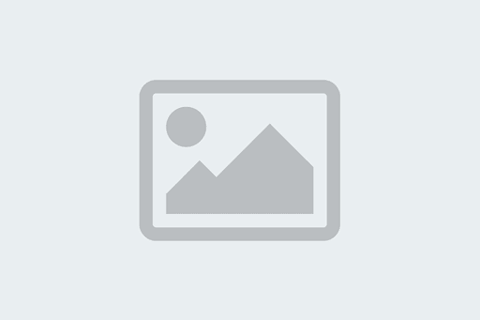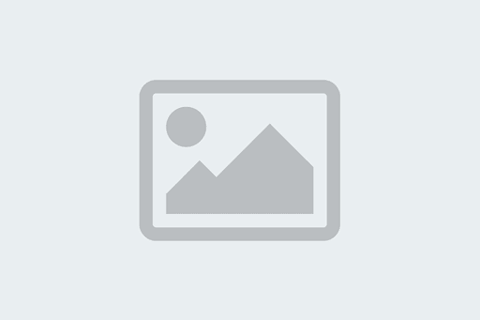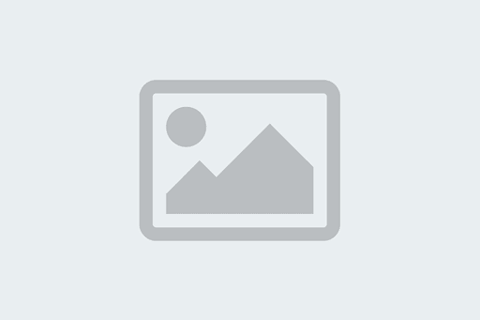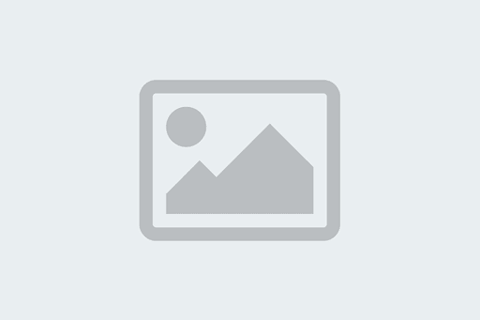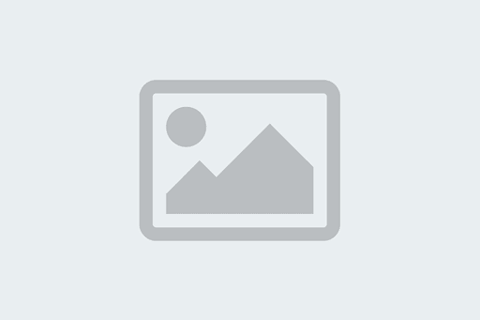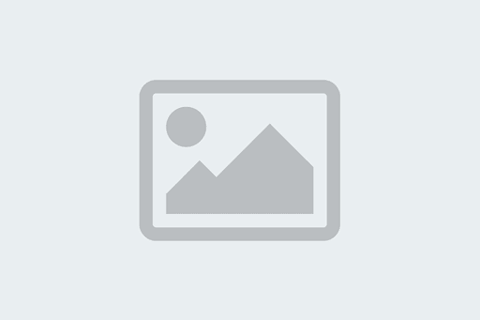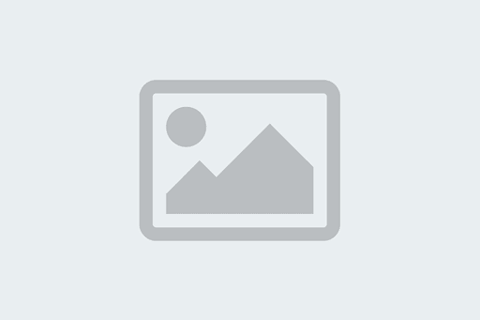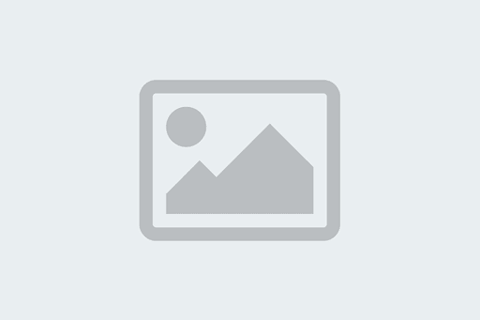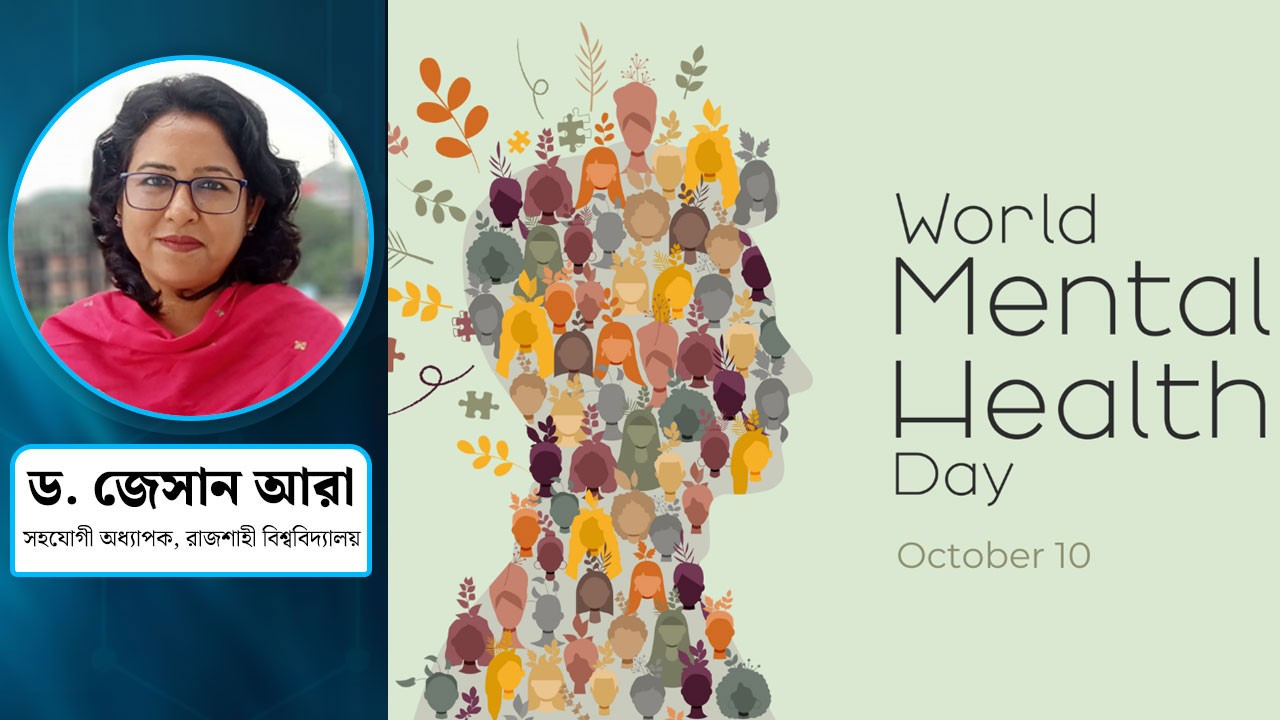
ড. জেসান আরা
মানসিক স্বাস্থ্য এমন একটি ক্ষেত্র, যা একজন মানুষের জীবনের প্রতিটা দিক শিক্ষা, কর্ম, সম্পর্ক, এমনকি সৃজনশীলতাকেও প্রভাবিত করে। তবু আমাদের সমাজে এটি এখনো প্রান্তিক, লজ্জার, এমনকি উপেক্ষিত একটি বিষয়। অথচ মানসিক সুস্থতা ছাড়া প্রকৃত অর্থে কোনো ব্যক্তিই পূর্ণাঙ্গভাবে ‘সুস্থ’ নয়।
বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার সংজ্ঞা অনুযায়ী, স্বাস্থ্য হলো শারীরিক, মানসিক, সামাজিক ও আবেগীয় অবস্থার সমন্বয়। এর মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্যই সেই ভিত্তি যা আমাদের চিন্তা, অনুভূতি ও আচরণকে ভারসাম্যপূর্ণ রাখে। এটি এমন একটি অবস্থা যেখানে ব্যক্তি তার জীবনের চাপ ও প্রতিকূলতা সামাল দিতে পারে, নিজের সক্ষমতা উপলব্ধি করতে পারে, শেখার ও কাজের দক্ষতা প্রদর্শন করতে পারে এবং সমাজে গঠনমূলক ভূমিকা রাখতে পারে।
মানসিক স্বাস্থ্য ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনের এমন এক মৌলিক উপাদান যা মানবিক সম্পর্ক, সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও সামষ্টিক অগ্রগতির ভিত্তি তৈরি করে। এটি কোনো বিলাসিতা নয়; বরং মানবজীবনের মৌলিক অধিকার। একজন মানুষ যেমন খাদ্য, বস্ত্র ও আশ্রয়ের অধিকার রাখে, তেমনি মানসিকভাবে সুস্থ থাকার অধিকারও রাখে।
বিজ্ঞাপন
বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য এখন একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। দ্রুত নগরায়ন, অর্থনৈতিক চাপ, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে। সর্বশেষ পরিসংখ্যান অনুযায়ী, বাংলাদেশের প্রায় ১৮.৭ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক মানসিক ব্যাধিতে ভুগছেন।
শিশু ও কিশোরদের ক্ষেত্রেও এটি আরও উদ্বেগজনক। প্রায় ১৪ শতাংশ শিশুর মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা রয়েছে। আর সবচেয়ে বড় সমস্যা হলো চিকিৎসা প্রাপ্তির ঘাটতি, যেখানে প্রায় ৭৫-৯২ শতাংশ প্রাপ্তবয়স্ক ও শিশু প্রয়োজনীয় মানসিক চিকিৎসা বা কাউন্সিলিং পাচ্ছে না।
বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্য এখন একটি বড় জনস্বাস্থ্য সমস্যা। দ্রুত নগরায়ন, অর্থনৈতিক চাপ, পারিবারিক টানাপোড়েন এবং সামাজিক পরিবর্তনের কারণে মানসিক রোগের প্রকোপ দিন দিন বাড়ছে।
এই চিকিৎসা-বঞ্চনার ফলে মানসিক রোগীরা প্রায়ই সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েন, আত্মসম্মান হারান, এমনকি আত্মহত্যার মতো মর্মান্তিক পরিণতির দিকেও ধাবিত হন। বাংলাদেশে ইতিমধ্যে Mental Health Act ২০১৮ আইন পাস হলেও তার বাস্তবায়নে কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো গড়ে ওঠেনি। তাই এখনো চিকিৎসক সংকট, পর্যাপ্ত অর্থায়ন, প্রশিক্ষণের অভাব ও সামাজিক কুসংস্কার বড় বাধা হিসেবে রয়ে গেছে।
২০২৫ সালের বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসের প্রতিপাদ্য বিষয়বস্তু হলো ‘সংকট ও দুর্যোগে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা প্রাপ্তি নিশ্চিত করা’। এই বিষয়বস্তু এমন এক সময়ের প্রতিফলন, যখন বিশ্বজুড়ে প্রাকৃতিক দুর্যোগ, সংঘাত, জলবায়ু পরিবর্তন ও মহামারির মতো সংকট মানুষের জীবন ও মানসিক স্থিতিশীলতাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করছে।
এইসব পরিস্থিতিতে শারীরিক সহায়তার পাশাপাশি মানসিক সহায়তা ও সেবা প্রাপ্তি সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ। দুর্যোগ, যুদ্ধ, বাস্তুচ্যুতি বা মহামারির মতো বিপর্যয় মানুষের জীবনে অনিশ্চয়তা, ভয়, শোক, ক্ষতি ও বিচ্ছিন্নতা তৈরি করে। এসব অভিজ্ঞতা থেকে জন্ম নেয় বিভিন্ন মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা, যেমন—
বিষণ্নতা (Depression): দীর্ঘস্থায়ী দুঃখবোধ, আত্মসম্মানহীনতা, ও জীবনের প্রতি আগ্রহহীনতা।
উদ্বেগজনিত ব্যাধি (Anxiety Disorders): অজানা ভয়, অতিরিক্ত দুশ্চিন্তা ও নিরাপত্তাহীনতা।
পোস্ট-ট্রমাটিক স্ট্রেস ডিসঅর্ডার (PTSD): দুর্ঘটনা, সহিংসতা বা দুর্যোগ-পরবর্তী ট্রমা, যা ঘুমের ব্যাঘাত, দুঃস্বপ্ন এবং মানসিক অস্থিরতা সৃষ্টি করে।
মনোসামাজিক চাপ (Psychosocial Stress): সামাজিক বিচ্ছিন্নতা, জীবিকা হারানো বা পরিবার থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার ফলে মানসিক ভারসাম্য নষ্ট হওয়া।
অর্থাৎ, দুর্যোগ বা জরুরি অবস্থায় মানসিক আঘাত অনেক সময় শারীরিক আঘাতের চেয়েও গভীর হয়। উদাহরণস্বরূপ কোভিড-১৯ মহামারির সময় বাংলাদেশসহ সারা বিশ্বে উদ্বেগ, বিষণ্নতা ও নিঃসঙ্গতার হার বৃদ্ধি পেয়েছিল। বহু মানুষ প্রিয়জন হারানোর শোক ও সামাজিক বিচ্ছিন্নতার কারণে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত হয়ে পড়ে।
একইভাবে, ঘূর্ণিঝড় বা বন্যার পর দেখা যায় মানুষ শারীরিকভাবে রক্ষা পেলেও মানসিক আঘাত থেকে মুক্ত হতে পারে না। এই আঘাতগুলো যদি সঠিকভাবে চিহ্নিত ও চিকিৎসা না করা হয়, তবে তা আত্মহত্যা, মাদকাসক্তি বা সামাজিক বিচ্ছিন্নতার মতো জটিলতায় রূপ নিতে পারে।
মানসিক স্বাস্থ্যসেবার প্রাপ্যতার চ্যালেঞ্জ
বিশ্বজুড়ে মানসিক স্বাস্থ্যসেবায় বড় বৈষম্য রয়ে গেছে। স্বাস্থ্য খাতের বাজেট প্রণয়নের সময় শারীরিক স্বাস্থ্য যতটা গুরুত্ব পায়, মানসিক স্বাস্থ্য তার তুলনায় অনেকটাই অবহেলিত থাকে। WHO-এর তথ্য অনুযায়ী, নিম্ন ও মধ্যম আয়ের দেশগুলোয় মানসিক স্বাস্থ্যসেবার জন্য বরাদ্দ স্বাস্থ্য বাজেটের ২ শতাংশেরও কম।
আর বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য খাতে মোট স্বাস্থ্য বাজেটের মাত্র ০.৪৪ শতাংশ বা ০.৫ শতাংশ বরাদ্দ করা হয়। যেমন ২০২২ সালে সরকারের মোট স্বাস্থ্য বাজেট ছিল ২.৩ বিলিয়ন মার্কিন ডলার, যার মধ্যে মানসিক স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ ছিল মাত্র ০.৫ শতাংশ। ২০২৪-২৫ অর্থবছর এবং পরবর্তী ২০২৫-২৬ অর্থবছরের বাজেটে বাংলাদেশের মানসিক স্বাস্থ্য খাতে বরাদ্দ মোট স্বাস্থ্য বাজেটের ১ শতাংশেরও কম।
এই বাজেট ঘাটতির কারণে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণের সুযোগ সীমিত হয়ে যাচ্ছে, যা মানসিক রোগের সময়মতো শনাক্তকরণ ও চিকিৎসায় বাধা সৃষ্টি করছে। মানসিক স্বাস্থ্য খাতে বাজেট বরাদ্দ বৃদ্ধি ও সেবা সম্প্রসারণের জন্য সরকারের নীতিগত সমর্থন ও কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ জরুরি। এতে করে মানসিক স্বাস্থ্য সেবা জনগণের কাছে আরও সহজলভ্য হবে এবং মানসিক রোগের বোঝা কমবে।
বাংলাদেশে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার উন্নয়নে বেশকিছু কাঠামোগত ও সামাজিক চ্যালেঞ্জ রয়েছে—
পর্যাপ্ত অর্থায়ন: মানসিক স্বাস্থ্য খাতে বাজেটের অভাবে সেবা প্রদান সীমিত হয়ে পড়ছে। দেশে মাত্র দুটি সরকারি মানসিক হাসপাতাল ঢাকার জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইন্সটিটিউট ও পাবনা মানসিক হাসপাতাল থেকে সেবা প্রদান করা হয়। রাজধানী বা বড় শহর ছাড়া গ্রামীণ এলাকায় মানসিক সহায়তা প্রায় অনুপস্থিত। দুর্যোগ-পরবর্তী এলাকায় শারীরিক চিকিৎসার ব্যবস্থা থাকলেও মানসিক পুনর্বাসন সচরাচর দেখা যায় না। ফলে আক্রান্ত জনগোষ্ঠী মানসিকভাবে দীর্ঘদিন বিপর্যস্ত অবস্থায় থাকে।
সেবার অপ্রতুলতা: দেশের অধিকাংশ জেলায় মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের ঘাটতি ভয়াবহ বাস্তবতা। এখনো দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক কাঠামো গড়ে উঠেনি, ফলে অসংখ্য মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত হচ্ছেন।
আর সরকারিভাবে যে মানসিক স্বাস্থ্যসেবা কার্যক্রমগুলো পরিচালিত হচ্ছে, সেগুলোর বেশিরভাগই পর্যাপ্ত অর্থায়নের অভাবে মারাত্মক সংকটে পড়েছে। উদাহরণস্বরূপ, বিভিন্ন জেলায় স্থাপিত ৩৫টি শিশু বিকাশ কেন্দ্র বর্তমানে বন্ধ হওয়ার পথে, যা অত্যন্ত উদ্বেগজনক।
এসব কেন্দ্রের স্বাভাবিক কার্যক্রম ব্যাহত হচ্ছে এবং সেবাগুলো কার্যত বন্ধ হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে। উল্লেখযোগ্য যে, এই কেন্দ্রগুলোয় প্রদত্ত বিশেষায়িত সেবাগুলো দেশের অন্য কোনো হাসপাতালে একসঙ্গে পাওয়া যায় না। কেন্দ্রগুলো যদি বন্ধ হয়ে যায়, তবে বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলার শিশুরা আর নিজ নিজ জেলাতেই মানসিক স্বাস্থ্য ও বিকাশ সংক্রান্ত সেবা নিতে পারবে না।
সময়মতো মানসিক সহায়তা না পেলে শৈশবকাল থেকে মানসিক সমস্যা আরও জটিল হবে এবং পরিপূর্ণ বিকাশে বড় বাধা তৈরি হওয়ার সম্ভাবনা বৃদ্ধি পাবে। এই বাস্তবতায় সরকারের দ্রুত হস্তক্ষেপ একান্ত প্রয়োজন।
মানসিক স্বাস্থ্য পেশাজীবীর অভাব: দেশে মানসিক রোগ বিশেষজ্ঞের সংখ্যা অত্যন্ত কম; প্রতি ১০ লাখ মানুষের জন্য মাত্র ২ জন মনোরোগ বিশেষজ্ঞ রয়েছেন। মনোবিজ্ঞানী, কাউন্সিলর ও সাইকিয়াট্রিক নার্সের তীব্র ঘাটতি মানসিক স্বাস্থ্য সেবা পৌঁছাতে প্রতিরোধ সৃষ্টি করছে।
আর্থিক সীমাবদ্ধতা: মানসিক চিকিৎসা সাধারণত ব্যক্তিগত খাতে সীমাবদ্ধ, যা নিম্ন আয়ের মানুষদের নাগালের বাইরে। এছাড়াও মানসিক অসুস্থতাকে এখনো অনেকেই পাপ, অভিশাপ বা দুর্বলতার প্রতীক হিসেবে দেখে। ফলে মানুষ লুকিয়ে থাকে এবং অনেকেই প্রয়োজন হলেও সাহায্য চায় না।
গবেষণা ও তথ্যের ঘাটতি: পর্যাপ্ত গবেষণা না থাকায় বাস্তব চিত্র জানা বেশ কঠিন। স্থানীয় তথ্যের অভাবে প্রয়োজনীয় নীতি প্রণয়ন ও কার্যক্রম প্রণয়নে সময়মতো এবং কার্যকর সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়। মূলত সেবার ঘাটতিই মানুষকে প্রয়োজনীয় মানসিক স্বাস্থ্য সেবা গ্রহণে বাধাগ্রস্ত করে এবং মানসিক রোগের সময়মতো শনাক্তকরণ ও চিকিৎসা প্রক্রিয়াও কঠিন হয়ে পড়ে।
নীতিনির্ধারক ও সমাজের করণীয়
১. নীতিনির্ধারণী ফোরামে মানসিক স্বাস্থ্য: মানসিক স্বাস্থ্যকে ঘিরে বিদ্যমান আইন ও নীতিগুলো কার্যকর করার জন্য শুধুমাত্র কৌশলগত নির্দেশনাই যথেষ্ট নয়, প্রয়োজন পর্যাপ্ত আর্থিক সহায়তা ও প্রশাসনিক দায়বদ্ধতা।
নীতিনির্ধারণী পর্যায়ে মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে যেসব পরিকল্পনা গৃহীত হয়, সেগুলোর বড় একটি অংশই পেশাদার মনোবিজ্ঞানী বা ক্লিনিক্যাল এক্সপার্টদের পরামর্শ ছাড়া তৈরি হয়। ফলে বাস্তবমুখী হলেও প্রাসঙ্গিকতা হারানো নীতিমালা তৈরি হয়, যার প্রয়োগও ব্যর্থ হয়। পেশাজীবীদের দক্ষতা কাজে লাগিয়ে নীতিনির্ধারণে তাদের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করা হলে, একটি বাস্তবসম্মত ও কার্যকর পরিকল্পনা গড়ে তোলা সম্ভব হতো।
২. দুর্যোগ ব্যবস্থাপনায় মানসিক স্বাস্থ্য অন্তর্ভুক্ত করা: খাদ্য, পানি, ওষুধের পাশাপাশি মানসিক সহায়তাও জরুরি সহায়তার অংশ হতে হবে।
৩. পেশাজীবী প্রশিক্ষণ: কাউন্সিলর, সমাজকর্মী ও স্বাস্থ্যকর্মীদের ট্রমা-পরবর্তী মানসিক সেবা দেওয়ার প্রশিক্ষণ দিতে হবে।
৪. হেল্পলাইন ও টেলি-কাউন্সিলিং: সংকটকালে সহজে ব্যবহারযোগ্য হেল্পলাইন চালু থাকা আবশ্যক।
৫. সহানুভূতিশীল সমাজ গঠন: পরিবারের সদস্যদের মানসিক কষ্টে থাকা মানুষকে বোঝার ও সমর্থন দেওয়ার সংস্কৃতি গড়ে তুলতে হবে।
৬. সচেতনতা বৃদ্ধি: গণমাধ্যম, স্কুল ও কর্মক্ষেত্রে মানসিক স্বাস্থ্য শিক্ষা চালু করা প্রয়োজন।
মানসিক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব
মানসিক স্বাস্থ্যসেবার গুরুত্ব শুধু ব্যক্তিগত উন্নয়ন বা সামাজিক স্থিতিশীলতার জন্য নয়, বরং এটি একটি জাতির সামগ্রিক অগ্রগতির জন্যও অপরিহার্য। মানসিক সহায়তা মানুষকে তার জীবনের সংকটময় সময়গুলোয় সঠিকভাবে মোকাবিলা করার মানসিক দৃঢ়তা দেয়, যা তাকে নতুনভাবে গড়ে ওঠার সুযোগ করে দেয়। কেবল ব্যক্তিগত সুস্থতাই নয় বরং এটি পারিবারিক, সামাজিক ও পেশাগত জীবনের মানকেও উন্নত করে।
প্রথমত, চিকিৎসার মাধ্যমে ব্যক্তি নিজের আবেগ, চিন্তা ও আচরণকে ভালোভাবে বুঝতে শিখেন। অনেক সময় মানসিক সমস্যার মূল কারণ অচেতন মনে লুকিয়ে থাকে, যা একজন প্রশিক্ষিত মানসিক স্বাস্থ্য বিশেষজ্ঞ ধীরে ধীরে উন্মোচন করতে সাহায্য করেন। চিকিৎসা প্রক্রিয়ায় কাউন্সিলিং, থেরাপি বা ওষুধের সমন্বয়ে ব্যক্তি তার মানসিক চাপ নিয়ন্ত্রণের উপায় শেখে, উদ্বেগ বা বিষণ্নতার মাত্রা কমে আসে এবং মনোযোগ ও স্মৃতিশক্তির উন্নতি ঘটে।
দ্বিতীয়ত, নিয়মিত থেরাপি বা মনস্তাত্ত্বিক সহায়তা গ্রহণ করলে আত্মবিশ্বাস বৃদ্ধি পায়। ব্যক্তি নিজের জীবনের সিদ্ধান্তগুলো আরও সচেতনভাবে নিতে সক্ষম হয় এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের ক্ষমতা বাড়ে। অতীতের দুঃখ বা ব্যথা থেকে ধীরে ধীরে মুক্তি পেয়ে সে ভবিষ্যতের প্রতি নতুনভাবে আশাবাদী হয়। মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মাধ্যমে একজন ব্যক্তি তার আবেগ প্রকাশের স্বাস্থ্যকর উপায় শেখে, যা পারিবারিক সম্পর্ক ও সামাজিক যোগাযোগকে আরও দৃঢ় করে তোলে।
দেশের অধিকাংশ জেলায় মানসিক স্বাস্থ্য সেবাকেন্দ্রের ঘাটতি ভয়াবহ বাস্তবতা। এখনো দেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে মানসিক স্বাস্থ্যসেবার মৌলিক কাঠামো গড়ে উঠেনি, ফলে অসংখ্য মানুষ প্রয়োজনীয় সহায়তা থেকে প্রতিদিন বঞ্চিত হচ্ছেন।
তৃতীয়ত, চিকিৎসা গ্রহণ করলে শারীরিক স্বাস্থ্যের উপরও ইতিবাচক প্রভাব পড়ে। মানসিক চাপ কমে গেলে ঘুমের মান উন্নত হয়, ক্ষুধা ও শক্তি ফিরে আসে এবং দেহের রোগপ্রতিরোধ ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। গবেষণায় দেখা গেছে, মানসিকভাবে সুস্থ ব্যক্তিরা হৃদরোগ, উচ্চ রক্তচাপ ও অন্যান্য মানসিক-শারীরিক জটিলতায় কম ভোগেন।
চতুর্থত, পেশাগত জীবনে একজন মানসিকভাবে স্থিতিশীল মানুষ বেশি মনোযোগী, উদ্যমী ও সৃজনশীল হয়। সে দলগতভাবে কাজ করতে পারে, সমস্যার সমাধান খুঁজে বের করতে পারে এবং নেতৃত্ব প্রদানের সক্ষমতাও অর্জন করে। এর ফলে কর্মস্থলে তার দক্ষতা, প্রভাব ও স্থায়িত্ব বৃদ্ধি পায়।
সবশেষে, মানসিক চিকিৎসা নেওয়া সমাজে ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি তৈরি করে। যখন মানুষ দেখে কেউ মানসিক সমস্যার জন্য সাহায্য নিচ্ছে এবং সুস্থ হয়ে উঠছে, তখন অন্যরাও সাহায্য নিতে উৎসাহিত হয়। এতে সমাজে কুসংস্কার ও লজ্জাবোধ কমে যায় এবং মানসিক স্বাস্থ্যের প্রতি গ্রহণযোগ্যতা বাড়ে। তাই সময়মতো মানসিক চিকিৎসা গ্রহণ কেবল একজন ব্যক্তির জীবন বদলে দেয় না, বরং এটি একটি সুস্থ, সচেতন ও সংহত সমাজ গঠনের ভিত্তি স্থাপন করে।
মানসিক স্বাস্থ্য কেবল ব্যক্তিগত কল্যাণ নয়; এটি মানবিক বেঁচে থাকার অন্যতম শর্ত। দুর্যোগ বা সংকটের সময় মানুষ যখন সব হারায়, তখন মানসিক সমর্থনই তার পুনর্জীবনের শক্তি হয়ে ওঠে। তাই এখনই সময়, মানসিক স্বাস্থ্যকে জরুরি সহায়তার মূল অগ্রাধিকার হিসেবে প্রতিষ্ঠা করা।
এমন সমাজ গড়ে তোলা, যেখানে বিষণ্নতা, উদ্বেগ এবং অন্যান্য কোনো মানসিক স্বাস্থ্য সমস্যা লজ্জার বিষয় নয় বরং সাহায্য চাওয়াটা সাহসের প্রতীক। মানসিক স্বাস্থ্য বিষয়ে সচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে প্রতি বছর ১০ অক্টোবর বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবস পালিত হয়।
২০২৫ সালের প্রতিপাদ্য বিষয় আমাদের মনে করিয়ে দেয় দুর্যোগের সময় খাদ্য, পানি বা আশ্রয়ের মতোই মানসিক সহায়তাও অপরিহার্য। এই দিনটি আমাদের আহ্বান জানায় মানসিক স্বাস্থ্য যেন আর প্রান্তিক বিষয় না থাকে, বরং তা মানবিক প্রতিক্রিয়ার কেন্দ্রে স্থান পাক। এই বিশ্ব মানসিক স্বাস্থ্য দিবসে আমাদের অঙ্গীকার হোক ‘মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কথা বলবো, সাহায্য চাইবো, এবং কাউকে একা রেখে দেবো না’।
ড. জেসান আরা : সহযোগী অধ্যাপক ও চিকিৎসা মনোবিজ্ঞানী, মনোবিজ্ঞান বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়
jesan@ru.ac.bd